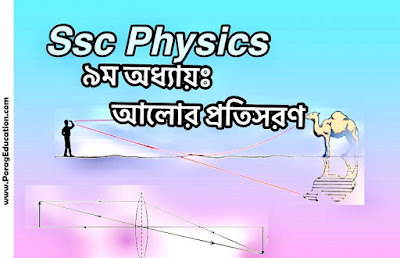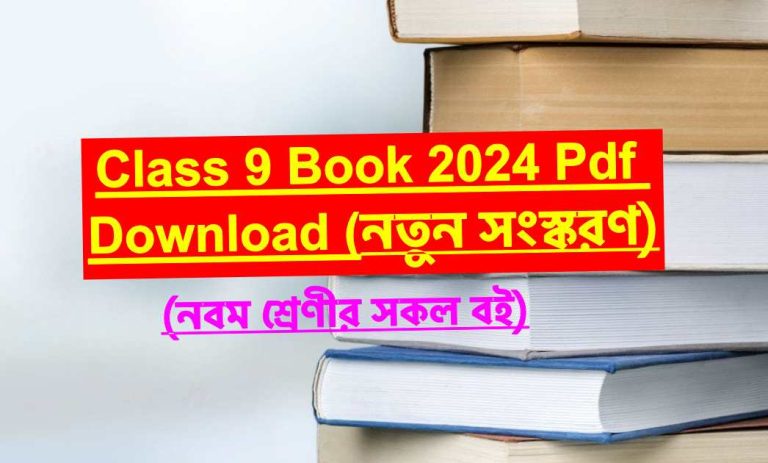Ssc Physics chapter 9 shortcut note
Ssc Physics chapter 9 shortcut note
৯ম অধ্যায়: আলোর প্রতিসরণ
৯ম অধ্যায়: আলোর প্রতিসরণ
আলোর প্রতিসরণ: আলোক রশ্মি এক স্বচ্চ মাধ্যম থেকে অন্য স্বচ্চ মাধ্যমে যাওয়ার সময়_ মাধ্যমদ্বয়ের বিভেদতলে তির্যকভাবে আপতিত রশ্মির দিক পরিবর্তনের ঘটনাকে আলোর প্রতিসরণ বলে।
*** প্রতিসরিত রশ্মির বেলায়: –ঘন থেকে হালকা মাধ্যমে অভিলম্ব থেকে দূরে সরে যাবে, —অন্যদিকে,হালকা থেকে ঘন মাধ্যমে অভিলম্বের দিকে বেকে যাবে।
সুত্র: প্রতিসরণের ১ম সুত্র: আপতিত রশ্মি,প্রতিসৃত রশ্মি,আপতিত বিন্দুতে বিভেদ তলের উপর অংকিত অভিলম্ব–একই সমতলে থাকে।
প্রতিসরণের ২য় সুত্র/স্নেলের সুত্র: একজোড়া নির্দিষ্ট মাধ্যম ও নির্দিষ্ট আলোর জন্য_(//১ম ও ২য় মাধ্যমের জন্য)_ আপতন কোণের সাইন ও প্রতিসরণ কোণের সাইনের অনুপাত সর্বদা ধ্রুব
অর্থাৎ η1sinθ1 = η2sinθ2
অর্থাৎ η1sinθ1 = η2sinθ2
অথবা,(2η1)= η1/η2= sin θ2/ sinθ1 = C2/C1 = λ2/λ1
এখানে, ২নং মাধ্যমের সাপেক্ষে ১নং মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্ক(2n1) নির্দেশ করছে।
*** যে মাধ্যমটি কম ঘন অর্থাৎ প্রতিসরণাঙ্ক কম হলে,তাতে আলোর বেগ বেশি।
বি:দ্র: মনে রাখবে,কোন মাধ্যমের আলোকীয় ঘনত্ব ও প্রাকৃতিক ঘনত্ব এক কথা নয়।
যেমন- প্রাকৃতিকভাবে (পদার্থের) ঘনত্ব হিসাব করলে, কেরোসিন(৮০০kgm-3) থেকে পানির(১০০০kgm-3) ঘনত্ব বেশি।
কিন্তু, আলোকীয় ঘনত্ব হিসাব করলে অর্থাৎ আলোর সাপেক্ষে, কেরোসিন(প্রতিসরণাঙ্ক ১.৪৪) থেকে পানির(প্রতিসরণাঙ্ক ১.৩৩) ঘনত্ব কম।
প্রতিসরণাঙ্ক: (এক স্বচ্ছ মাধ্যম হতে অপর স্বচ্ছ মাধ্যমে তির্যকভাবে আলোকরশ্মি প্রবেশ করলে,) আপতন কোণ ও প্রতিসরণ কোণের সাইনের অনুপাতকে ১ম মাধ্যমের সাপেক্ষে ২য় মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্ক বলে।
[ কোনো মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্ক,n=c/v ;
[ কোনো মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্ক,n=c/v ;
এখানে, c হচ্ছে আলোর বেগ এবং
v হচ্ছে ঐ মাধ্যমের বেগ। ]
v হচ্ছে ঐ মাধ্যমের বেগ। ]
কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমের আলোর প্রতিসরণাঙ্ক(n) এর মান:-
|
শুন্য মাধ্যম-১
|
বাতাস- ১(প্রায়)
|
পানি-১.৩৩
|
কাচ-১.৫২।
|
হীরা-২.৪২
|
অপটিক্যাল ফাইবার-১.৫
|
প্রতিসরণাঙ্ক দুই প্রকার।যথা-
আপেক্ষিক প্রতিসরণাঙ্ক: এক স্বচ্ছ মাধমের সাপেক্ষে অপর কোন স্বচ্ছ মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্ককে আপেক্ষিক প্রতিসরণাঙ্ক বলে।
পরম প্রতিসরণাঙ্ক: শুন্য মাধ্যমের সাপেক্ষে অপর কোন (স্বচ্ছ) মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্ককে পরম প্রতিসরণাঙ্ক বলে।
# বায়ু অপেক্ষা পানির প্রতিসরণাঙ্ক১.৩৩ বলতে কি বুঝায়?
প্রতিসরণাঙ্ক এর বৈশিষ্ট্য:-
১) আলোক রশ্মি যে মাধ্যমে প্রবেশ করে,প্রতিসরণাঙ্ক হয় সেই মাধ্যমের। যে মাধ্যম থেকে আসে সে মাধ্যমের সাপেক্ষে।
২)প্রতিসরণাঙ্ক আপতন কোণের উপর নির্ভর করে না,কেবল মাধ্যমদ্বয়ের প্রকৃতি ও আলোর রঙের উপর নির্ভর করে।
*** লাল আলোর প্রতিসরণাঙ্ক এর সবচেয়ে কম,বেগুনি আলোর সবচেয়ে বেশি।
ক্রান্তি কোণ/সংকট কোণ: আপতন কোণের যে মানের জন্য প্রতিসরণ কোণ ৯০` হয়,ঐ আপতন কোণকে ক্রান্তি কোণ বলে। @c=sin–1(n1/n2)
শর্ত: আলোটা ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে যাবে।
শর্ত: আলোটা ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে যাবে।
#প্রশ্ন: হীরকের সংকট কোণ 24′ বলতে কি বুঝায়?
পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন: আপতন কোণের যে মানের জন্য প্রতিসরণ কোণ ৯০` হয়,ঐ আপতন কোণকে ক্রান্তি কোণ বলে। এখন, ক্রান্তি কোণের আপতন কোণের মানটা যদি বাড়ানো হয়,তাহলে আলো প্রথম মাধ্যমে ফিরে আসে(/প্রতিফলিত হয়),একে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন বলে।
শর্ত: ১)আলোটা ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে যাবে।
২)আপতন কোণের মানটা ক্রান্তি কোণের চেয়ে বেশি হবে।
উদাহরণ:-
১)মরিচিকা: মরিচিকা অর্থ দৃষ্টিভ্রম। মরুভূমি অঞ্জলে ভুল প্রতিবিম্ব দেখার মাধ্যমে (এ ধরনের) দৃষ্টিভ্রম দেখাকে(/ঘটে যাকে) মরিচিকা বলে। মরিচিকা দূর থেকে দেখা যায়,কাছ থেকে দেখা যায় না।
ব্যাখ্যা/কার্যপদ্ধতি:
→ দিনের বেলায় সুর্যের তাপে মরুভূমির বালি অনেক উত্তপ্ত থাকে। ফলে মরুভূমির বালি সংলগ্ন/কাছাকাছি বায়ুস্তর অপেক্ষাকৃত হালকা হয় বলে নিচের বায়ুস্তরের ঘনত্ব ও প্রতিসরণাঙ্ক কম হয় । অন্যদিকে, উপরের বায়ুস্তর অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা হয় বলে উপরের বায়ুস্তরের ঘনত্ব ও প্রতিসরণাঙ্ক বেশি হয় । এভাবে মরুভুমির বায়ুর দুইটা স্তর সৃষ্টি হয়।
→ এখন, কোন গাছ থেকে আলোক রশ্মি পথিকের চোখে আসার সময় উপরের অপেক্ষাকৃত হালকা বায়ুস্তর থেকে নিচের অপেক্ষাকৃত ঘন বায়ুস্তরের দিকে বাকতে বাকতে আপতিত রশ্মিটা এমন একটা কোণে বেকে যায় যেটা ক্রান্তি কোণের চেয়ে বড় মানের কোণে আপতিত হয়। ফলে আলোটা পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলিত হয়ে আবার উপরের ঘন বায়ু মাধ্যমে ফিরে আসে এবং ঐ জায়গায় গাছটির উলটো প্রতিবিম্ব দেখা যায়। তাই পথিকের চোখে মনে হয় ঐ জায়গায় বুঝি পানি/জলাশয় আছে।
এভাবে কোনো পথিক মরুভূমিতে চলার সময় দুরবর্তী কোনো গাছকে সরাসরি দেখার পাশাপাশি প্রতিবিম্ব আকারেও দেখতে পায়। এভাবে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের মাধ্যমে দৃষ্টিভ্রম দেখার ফলে মরিচিকা সৃষ্টি হয়।
২)অপটিক্যাল ফাইবার: অপটিক্যাল ফাইবার হচ্ছে সরু কাচের তন্তু যার ভেতর দিয়ে উচ্চ গতিতে ডেটা/তথ্য পাঠানো হয়।
ব্যাখ্যা/কার্যপদ্ধতি: এর ভেতরের অংশকে কোর(core) বলে যেটার প্রতিসরণাঙ্ক অনেক বেশি হয় অর্থাৎ ভেতরের অংশটি ঘন মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।
এর বাহিরের অংশকে ক্লাড(clad) বলে যেটার প্রতিসরণাঙ্ক অপেক্ষাকৃত কম হয় অর্থাৎ বাহিরের অংশটি হালকা মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।
এখন আলো কোর(core) এর ভেতর দিয়ে পাঠালে সেটার পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ঘটবে এবং কোর এর মধ্যে আলোটা আটকা পড়ে অনেক দূর পর্যন্ত চলতে থাকবে। এভাবে অফটিক্যাল ফাইবার দিয়ে আলোকে খুব দ্রুত শত শত মাইল পাঠানোর মাধ্যমে উচ্চ গতিতে ডাটা/তথ্য পাঠানো যায়।
বি:দ্র: দৃশ্যমান আলোর শোষণ বেশি হওয়ায় এক্ষেত্রে লম্বা/দৈর্ঘ্য তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অবলাল আলোক রশ্মি ব্যবহার করা হয়।
৩) রংধনু:সূর্যের সাদা আলো মেঘের পানির মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় বিভিন্ন রংে বিভক্ত হওয়াকে,।
ব্যাখ্যা/কার্যপদ্ধতি: basic-সূর্যের সুর্যের আলো মেঘেরপানিতে পড়লে সুর্যের সাদা আলো বিভিন্ন রঙে প্রিজমের মত বিভক্ত হয়ে রংধনু সৃষ্টি করে।
লেন্স: দুটি গোলীয় তল অথবা একটি গোলীয় তল ও অপরটি সমতল পৃষ্ঠ দ্বারা সীমাবদ্ধ স্বচ্চ প্রতিসারক(/আলোক) মাধ্যমকে লেন্স বলে।
২)গোলীয় তল দ্বারা লেন্স ২প্রকার:
–২.১উত্তল: যে লেন্সের উভয় তলই উত্তল বা মধ্যভাগ মোটা এবং প্রান্তভাগ সরু,তাকে উত্তল লেন্স বলে।
এটি তিন প্রকার: উভত্তল,সমতলোত্তল অবতলোত্তল।
–২.২অবতল:যে লেন্সের উভয় তলই অবতল অথবা মধ্যভাগ সরু এবং প্রান্তভাগ মোটা,তাকে উত্তল লেন্স বলে।
এটিও তিন প্রকার: উভাবতল,সমাবতল,উত্তলাবতল।
# উত্তল লেন্স ও অবতল লের্ন্সের পার্থক্য লিখ।
মনে রাখবে,
# অভিসারী ক্রিয়াহচ্ছে আপতিত আলোক রশ্মি প্রতিসরণের পর এক বিন্দুতে মিলিত(/কেন্দ্রীভূত/অভিসারিত) হবে। <অবতল দর্পণ+উত্তল লেন্স >
# অপসারী ক্রিয়া হচ্ছে আপতিত আলোক রশ্মি প্রতিসরণের পর ছড়িয়ে পড়বে,কখনো মিলিত হয় না।
<উত্তল দর্পণ +অবতল লেন্স>
<উত্তল দর্পণ +অবতল লেন্স>
# দর্পন চেনার উপায় ব্যাখ্যা কর।
# সমতল দর্পনে লম্বভাবে আপতিত আলোকরশ্মি একই পথে ফিরে আসে কেন?
# সেলুনে সমতল দর্পন ব্যবহার করা হয় কেন?
# উত্তল লেন্সকে অভিসারী লেন্স বলা হয় কেন?
চিকিৎসাক্ষেত্রে অবতল দর্পন ব্যবহার করা হয় কেন?
# অবতল দর্পনকে অভিসারী এবং উত্তল দর্পনকে অপসারী দর্পন বলা হয় কেন-ব্যাখ্যা কর।
# লেন্স/দর্পনের ব্যবহার: পুরাতন বই দেখ ১৩৭পৃষ্ঠা
যমতল দর্পন চেহারা দেখা/রুপচর্চা,টেলিস্কোপ; চশমা,মাইক্রোস্কোপ,ভিডিও প্রজেক্টর,ক্যামেরা ইত্যাদিতে।
# দর্পন ও লেন্স এর প্রয়োজনীয় রাশিসমুহ ও বৈশিষ্ট্যসসহ ব্যাখ্যা:
বক্রতার কেন্দ্র: গোলীয় দর্পন যে গোলকের অংশবিশেষ _সে গোলকের কেন্দ্রকে বক্রতার কেন্দ্র বলে।
বক্রতার ব্যাসার্ধ:(f = r/2 বা, r=2f) গোলীয় দর্পন/লেন্স যে গোলকের অংশবিশেষ _সে গোলকের ব্যাসার্ধকে বক্রতার ব্যাসার্ধ বলে।
মেরু বিন্দু: গোলীয় দর্পনের প্রতিফলক পৃষ্ঠের মধ্যবিন্দুকে মেরু বলে।
আলোক কেন্দ্র: লেন্সে আপতিত রশ্মির সমান্তরালে নির্গত প্রতিসরিত রশ্মি (লেন্সের প্রধান অক্ষের উপরস্থ) যে বিন্দু দিয়ে যায়,তাকে আলোক কেন্দ্র বলে।
প্রধান অক্ষ: গোলীয় দর্পন/লেন্স এর_ বক্রতার কেন্দ্র ও মেরু বিন্দুর/আলোক কেন্দ্রর মধ্যদিয়ে গমনকারী সরলরেখাকে প্রধান অক্ষ বলে।
গৌণ অক্ষ: গোলীয় দর্পন/লেন্স এর_ বক্রতার কেন্দ্র ও মেরু বিন্দু ব্যতিত অন্য যেকোন বিন্দুর মধ্যদিয়ে গমনকারী সরলরেখাকে গৌণ অক্ষ বলে।
→(প্রধান) ফোকাস: (f=r/2) গোলীয় দর্পন/লেন্স এ _প্রধান অক্ষের নিকটবর্তী ও সমান্তরাল আপতিত রশ্মি গুলো_ প্রতিফলনের পর প্রধান অক্ষের যে বিন্দুতে মিলিত হয়,তাকে প্রধান ফোকাস বলে।
→ফোকাস দুরুত্ব: আলোক কেন্দ্র বা মেরু বিন্দু থেকে প্রধান ফোকাস পর্যন্ত দুরুত্বকে ফোকাস দুরত্ব বলে।
লেন্সের প্রথম ও দ্বিতীয় পৃষ্ঠ:
যে পৃষ্ঠ দিয়ে আলোক রশ্মি লেন্সের মধ্যে প্রবেশ করে(/আপতিত হয়) সেটি লেন্সের প্রথম পৃষ্ঠ এবং যেটি দিয়ে বেরিয়ে যায়(/প্রতিসরিত হয়) সেটি লেন্সের দ্বিতীয় পৃষ্ঠ।
#চোখের ত্রুটির প্রকারভেদ,কারণ ও প্রতিকার:-
প্রকারভেদ-
চোখের ত্রুটি দুই ধরনের:
১। ক্ষীণ দৃষ্টি:
কারণ- চোখের লেন্সের অভিসারি ক্রিয়া বেড়ে গেলে ক্ষীণ দৃষ্টি সৃষ্টি হয়।
প্রতিকার– অবতল লেন্সের ক্রিয়া অপসারী হওয়ায় অবতল লেন্সের সাহায্যে চোখের চোখের অভিসারী ক্রিয়ার মান কমানো যায়। তাই ক্ষীণ দৃষ্টি প্রতিকারে অবতল লেন্স ব্যবহার করা হয়।
প্রকারভেদ-
চোখের ত্রুটি দুই ধরনের:
১। ক্ষীণ দৃষ্টি:
কারণ- চোখের লেন্সের অভিসারি ক্রিয়া বেড়ে গেলে ক্ষীণ দৃষ্টি সৃষ্টি হয়।
প্রতিকার– অবতল লেন্সের ক্রিয়া অপসারী হওয়ায় অবতল লেন্সের সাহায্যে চোখের চোখের অভিসারী ক্রিয়ার মান কমানো যায়। তাই ক্ষীণ দৃষ্টি প্রতিকারে অবতল লেন্স ব্যবহার করা হয়।
২। দুরদৃষ্টি:
কারণ- চোখের লেন্সের অভিসারি ক্রিয়া কমে গেলে ক্ষীণ দৃষ্টি সৃষ্টি হয়।
প্রতিকার– উত্তল লেন্সের ক্রিয়া অভিসারী হওয়ায় উত্তল লেন্সের সাহায্যে চোখের চোখের অভিসারী ক্রিয়ার মান বাড়িনো যায়। তাই ক্ষীণ দৃষ্টি প্রতিকারে অবতল লেন্স ব্যবহার করা হয়।
কারণ- চোখের লেন্সের অভিসারি ক্রিয়া কমে গেলে ক্ষীণ দৃষ্টি সৃষ্টি হয়।
প্রতিকার– উত্তল লেন্সের ক্রিয়া অভিসারী হওয়ায় উত্তল লেন্সের সাহায্যে চোখের চোখের অভিসারী ক্রিয়ার মান বাড়িনো যায়। তাই ক্ষীণ দৃষ্টি প্রতিকারে অবতল লেন্স ব্যবহার করা হয়।
SSC Physics chapter 8 Shortcut note pdf download; click_here